X


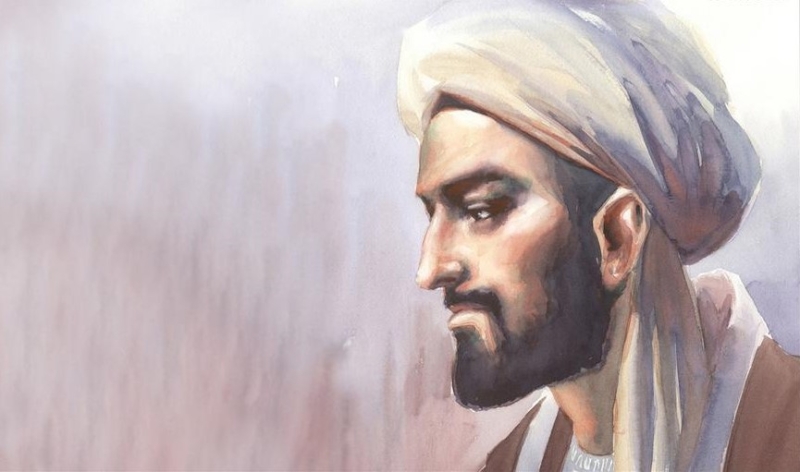
ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে সর্বত্র সমানভাবে সমাদৃত। ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেও এই মুসলিম মনীষী চিন্তায়, চেতনায়, জ্ঞান সাধনায় আধুনিক যুগ ও সভ্যতার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে গিয়েছেন। ঐতিহাসিক, রাজনীতিক ও সমাজ-দার্শনিক ইবনে খালদুনের জন্ম ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে তিউনিস-এর এক বনেদি অভিজাত পরিবারে। তাকে নিয়ে লিখেছেন অন্বেষক-ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ।
ভূমিকা
ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে সর্বত্র সমানভাবে সমাদৃত। ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেও এই মুসলিম মনীষী চিন্তায়, চেতনায়, জ্ঞান সাধনায় আধুনিক যুগ ও সভ্যতার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে গিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন. স্মিড তাঁর ‘ইবনে খালদুন, হিস্টোরিয়ান, সোশ্যালিস্ট অ্যান্ড ফিলোসফার’ (নিউইয়র্ক, ১৯৩০, পৃ. ১৫-১৬) নামক গ্রন্থে তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। (হদিশ, আখতার-উল আলম, ইবনে খালদুন : জীবনী ও চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।)
পরিচয়
ঐতিহাসিক, রাজনীতিক ও সমাজ-দার্শনিক ইবনে খালদুনের জন্ম ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে তিউনিস-এর এক বনেদি অভিজাত পরিবারে। হিজরি সাল হিসেবে সেটি ৭৩২ হিজরি, ১ রমজান। তাঁর পারিবারিক প্রকৃত নাম ওয়ালিউদ্দিন আবদুর রহমান। যদিও তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে ইবনে খালদুন নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁকে তাবৎ দুনিয়া চেনে জানে এইভাবে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ এবং শ্রেষ্ঠ সমাজ-দার্শনিক হিসেবে। (প্রাগুক্ত; পৃ. ২)
গৌরবময় তিউনিস
উত্তর আফ্রিকার তিউনিস সেই সময়ে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। শৈশবে ইবনে খালদুন তাঁর পিতার কাছেই পাঠাভ্যাস শুরু করেন। কুরআনে হাফিজ হন। তফসির, হাদিস, ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন পরবর্তীতে। তিউনিস-এর বিদ্বৎসমাজ সেই সময়ে জ্ঞানচর্চায় ব্যাপক সুখ্যাতি আর সুনাম অর্জন করেন। এই পণ্ডিত মহলের কিয়দংশের কাছে ইবনে খালদুন ইতিহাস সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে পাঠ খতম করেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ছন্দ ইত্যাকার বিষয়েও পারদর্শিতা অর্জন করেন। কোনও বিষয়কে ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করার মতো ক্ষমতা ছিল তাঁর স্বভাবজাত। উপরন্তু তিউনিস-এর পণ্ডিতবর্গ তাঁর চিন্তার দিগন্তটিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর উপরে তাঁর শিক্ষকবর্গের প্রভাব ছিল অপরিসীম।
জীবন: সৃজনকাল
ইবনে খালদুন তাঁর লেখাজোখার মধ্যে কোন শিক্ষকের কাছে কি পড়েছেন, কি শিখেছেন, তাঁর পড়ানোর বৈশিষ্ট্য কি— তাও পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে গিয়েছেন। মনুষ্য চরিত্রকে অনুধাবন করা বা বিশ্লেষণের ধারাটি তাঁর একান্ত স্বোপার্জিত। এর ফলেই তাঁর মগজাস্ত্রে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ ধরনের তাত্ত্বিক একটি প্রকাশ লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। জীবনে প্রাথমিক ১৮ বছর শিক্ষার্জনেই অতিবাহিত হয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার আরও আগ্রহ ও ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু এই সময়েই তিউনিস-এ প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর পিতা-মাতা, এমনকি খালদুনের প্রিয় শিক্ষকরাও আর বেঁচে ছিলেন না। তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। বিদ্যাচর্চার বিষয়টিও থমকে যায়। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিউনিস-এর শাসকের সহযোগিতায় মোহর-রক্ষীর দায়িত্ব পান। এমনবিধ দায়িত্বে ইবনে খালদুন তৃপ্ত হচ্ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব পরিচয়কে বৃহত্তর দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে আগ্রহী ছিলেন। দুনিয়াকেও জানতে চাইছিলেন।
আত্মপ্রতিষ্ঠার খোঁজে
নানান পরিস্থিতিজাত কারণে ইবনে খালদুন তিউনিস পরিত্যাগ করেন এবং ৭৫৫ হিজরিতে ফেজ নামক একটি ‘প্রিন্সলি স্টেট’-এর উলামা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর কর্মদক্ষতার গুণে ফেজের সুলতানের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন। সুলতানের ‘Confidential Advisor’ পদে উন্নীত হন। শুধু তাই নয়, রাজকীয় সিলমোহর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও খালদুনের ওপর বর্তিত হয়। ক্রমেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কর্মোদ্যোগী ইবনে খালদুন সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেন। উত্তর আফ্রিকার যথার্থ প্রতাপ সম্পন্ন শাসক সুলতান আবু এনান-এর সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক তাঁকে ক্ষমতাধর করে তোলে। সেই সুবাদে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যাঞ্চল ভ্রমণের ফলে তিনি সুপরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এই ৩০ বছরে লেখাপড়ার অসীম সুযোগ পেয়েছিলেন। অগণন জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে আন্তরিক আলাপ-আলোচনার সুযোগ পান। উপরন্তু আন্দালুসিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার বিদ্বৎসমাজের বৃহদাংশ তখন ফেজ নগরীতে এসে বসবাস এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা আর অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত চিলেন। এই শ্রেণির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অতীব হার্দিক। এই মওকায় ইবনে খালদুন নিজ জ্ঞান ও মনীষার বিকাশে যত্নবান হয়ে ওঠেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কথা, রাষ্ট্র আর সমাজের কথা এবং জ্ঞানগত বিশ্বের ইতিহাস নিয়ে নিরন্তর চর্চার মধ্যে ছিলেন। এর ফলেই তাঁর ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিপুল রচনা সম্ভার রেখে যেতে পেরেছেন। তাঁর জীবনের চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আখতার-উল আল ‘ইবনে খালদুন’ নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, কখনও তাঁর স্থান হয়েছে যশ-খ্যাতির উচ্চতম আসনে, কখনও বা তাঁর সৌভাগ্য সূর্য দূর অস্তাচলের শেষ সীমানায় বিলীন হয়ে গেছে। কখনও ধন-দৌলত তাঁকে শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্যশালীরূপে প্রতিপন্ন করেছে, কখনও বা দারিদ্রের নিদারুণ কষাঘাত তাঁকে নিক্ষেপ করেছে দুরবস্থার চরমতম অধঃপাতে। (পৃ. ১৪)
আরও সামনে এগিয়ে চলো
ইবনে খালদুনের জীবনের চলিষ্ণুতায় ছিল প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। ৭৬৪ হিজরিতে তিনি গ্রানাডা হিজরত করলেন্ আন্দালুসিয়ার সুলতান মুহাম্মদ খালদুনকে মর্যাদা আর গুরুত্বসহকারে তাঁর মন্ত্রীপরিষদের সদস্য নির্বাচিত করলেন। এখানেও প্রতিভা আর ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ পেলেন। সুস্থির হয়ে বসবাস করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে আবারও নয়া গন্তব্যের জন্য আল্-মেবিয়া নামক বন্দর থেকে সমুদ্রপথে পাড়ি জমালেন।
ফেজ-এ প্রত্যাবর্তন
রোমাঞ্চকর জীবনযাপনের পর ইবনে খালদুন জীবনের আখরি পর্যায়ে আবার ফেজ-এ ফিরলেন। উজির ইবনে গাজি তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলেন। বেশ কয়েক বছর শাসক গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা জরুরি ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর শলা-পরামর্শকে উপেক্ষা করার তাকত কারুরই ছিল না। আদতে তাঁর মগজটাই ছিল আলাদা ধাঁচের। খালদুনের জীবনে অবসর বলে কোনও শব্দ ছিল না। কিন্তু এই সময়ে প্রায় চার বছর বেশ স্বস্তির সঙ্গে যাপন করছিলেন। এতাবৎকাল অর্জিত জ্ঞান-প্রজ্ঞা আর অশেষ পরিশ্রমের ফসল হিসেবে বিশ্ববাসী পেলেন ভুবন বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মুকাদ্দামা।’ জীবনের নানা কিসিমের অভিজ্ঞতাজাত উপাদানগুলো লিখিতভাবে এই প্রথম তৎকালীন জনসমক্ষে এল। তাঁর চিন্তাজাত তত্ত্বাদর্শ আজও উঁচু স্থানে অবস্থানের যোগ্য হয়ে রয়েছে। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চ গুণমানের ক্ষেত্রে খালদুনের ইতিহাস— সমাজবিজ্ঞান নির্ভর তাত্ত্বিক এই নির্মাণ আজও আদম সভ্যতার সামনে আলোকবর্তিকার ন্যায় প্রতিভাত হয়। ‘মুকাদ্দামা’র রচনাকাল ছিল ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর আর একটি অনন্য সাধারণ সৃষ্টি হল— ‘কিতাব-উল্-ইবার।’ সাতটি খণ্ডে গ্রন্থটি রচিত। তাঁর অন্য আর একটি গ্রন্থ ‘আল-তারিফ।’ সাদিয়োকাল থেকে আরব জাতির যে ইতিহাস তিনি রচনা করেছিলেন তা তাঁর ‘তোওয়ারিখ নামক গ্রন্থে রয়েছে।
পুনশ্চ: তিউনিস
ইবনে খালদুন ফিরলেন তাঁর যৌবনের বিকাশভূমি তিউনিস-এ। তাঁর প্রায় অসাধ্য সাধনার বিষয়গুলো সাজিয়ে নিলেন এখানে এসে। তিনি কি লিখলেন? আরব জাতির ইতিহাস, বার্বারদের ইতিবৃত্ত, প্রাক্-ইসলামি জীবন, ইসলাম পরবর্তী জীবন, প্রাচ্যের মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, প্রাচীন নানা দেশ, বহুবিধ জাতির ইতিহাস, খ্রিস্টান জাতির সুদীর্ঘ ইতিবৃত্ত, শাসন আর রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচয়।
হজব্রত পালনের জন্য
ইবনে খালদুনের পায়ের তলায় যেন সরষে ছিল। আবারও তিনি বৃদ্ধ বয়সে হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি তিউনিস ত্যাগ করলেন। বস্তুত আর তাঁর তিউনিসে ফেরার সুযোগ হয়নি। ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছলেন। সেখান থেকে কায়রোতে হাজির হলেন। কায়রোর উচ্চমানের জীবনযাপন তাকে চমকিত করেছিল। আদতে তিনি ছিলেন আফ্রিকার মরু অঞ্চলের বাসিন্দা। কায়রোর বিদ্বৎসমাজ তাঁকে খাতিরের নজরে দেখতেন। ছাত্ররা তাঁর অধ্যাপনায় বিমোহিত হয়ে যেত। পণ্ডিতবর্গ তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে ইন্তেজার করতেন। বস্তুত প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্য উভয় সভ্যতার বিদ্বজ্জন তাঁর মেধা আর মমন এবং বিশ্লেষণাত্মক লেখার স্টাইলে মোহিত হয়েছিলেন। শিক্ষায়তনগুলো ছিল অভিজাত আর মর্যাদাবাহী।
বর্ণময় জীবন: বিচিত্র অভিজ্ঞতা
ইবনে খালদুন তাঁর আত্মস্মৃতিকথায় জীবনের নানান অভিজ্ঞতা আর ঘাত প্রতিঘাতের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ‘চেকার্ড’ জীবনের কথা— সেই দেশ-সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুঝতে সহায়ক হয়ে ওঠে। খালদুনের জীবনী লেখক আখতার-উল-আলম মন্তব্য করেছেন, সমাজ দর্শনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, জীবনীশক্তি (আল্-আশারিয়া), রাষ্ট্রিক শক্তির স্থিতি, সভ্যতা ও ঐশ্বর্যের বিকাশ, শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব, সঞ্জীবনী শক্তির ক্রমবিকাশ এবং এ সবের পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পৃক্ত ছিলেন। এর ফলে বিভিন্ন দেশের শাসক গোষ্ঠীর হয়ে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনেও ক্ষিপ্রতার পরিচয় দেন। মিশরীয় সুলতানের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার সুলতানদের মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী ও সক্রিয় ছিলেন। কূটনৈতিক দক্ষতারও পরিচয় রেখেছিলেন। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইবনে খালদুন জেরুসালেম সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর বিস্তৃত বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। মসজিদে আকসা, মকবরা-ই-খালিশ আর বেথেলহেমের সৌধমালা সম্পর্কে যথার্থ ইতিহাসের সন্ধান দিয়েছেন। ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কায়রো প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কি অসাধারণ প্রাণশক্তি ছিল ইবনে খালদুনের ভেবে চমকিত হতে হয়। বিদেশ সফর শেষে ইবনে খালদুন ৮০২ হিজরিতে কায়রো ফিরে আসেন। এই সবের বর্ণনা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, শাসক বর্গের শাসনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা রীতিমতো রোমাঞ্চকর।
তৈমুরের সঙ্গে মুলাকাত
ইবনে খালদুনের জীবনের একটি চমকপ্রদ আর কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে — দুর্দমনীয় অভিযানকারী তৈমুর লঙের সঙ্গে তাঁর মুলাকাত এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ। এই সাক্ষাতের বিষয়টি খুব স্পষ্ট এবং সোজাসুজিভাবে বলেছেন, তাঁর ‘আত্তারীফ’ নামক গ্রন্থে। একটি বিশাল সুসজ্জিত তাঁবুর মধ্যে তৈমুর লঙের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই তুলনারহিত ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি ইবনে খালদুন আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। তৈমুর লঙ ব্যাপক সময় ধরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ব্যক্তিগত খবর, মিশর থেকে তাঁর আসার কারণ ইত্যাদি ছাড়াও তৈমুর তাঁর নিকট থেকে উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহ, তাদের শহর-বন্দর ও অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। পরিশেষে উত্তর আফ্রিকার উপরে একখানি পুস্তক রচনার জন্য তিনি খালদুনকে নির্দেশ দেন। খালদুনও তৈমুরের নিকট তার সমাজবিষয়ক নিজস্ব মতবাদ সমূহ এবং রাষ্ট্রের মূল শক্তি, উত্থান-পতন, তার সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। খালদুন তৈমুরের সমীপে দেওয়া ওয়াদা পালন করেছিলেন। উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে ১২ খানি ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করেন এবং সেগুলো মহামান্য তৈমুরকে প্রদান করা হয়। তৈমুর যোগ্য সম্মান দিয়েছিলেন। পুস্তিকাগুলো মঙ্গোলিয়ান ভাষায় তৈমুর তরজমা করিয়েছিলেন।
মুকাদ্দামার বিষয়
বিশ্বের তাবৎ সভ্য দেশের ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী আর রাষ্ট্রবেত্তারা ইবনে খালদুনের ‘মুকাদ্দামা’ (Preleogmena) নামক গ্রন্থটিকে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের এক মহাসূত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কি আছে এই গবেষণাকর্মটিতে। সেটি বলা যাক: ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের মুখমন্ধ অর্থাৎ ‘মুকাদ্দামা’য় সার্বভৌমত্ব, মুদ্রা ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় করের প্রকৃতি, সাম্রাজ্যের পতনে এবং পাশ্চাদপদতায় অবিচার আর বৈষম্যের প্রভাব, জুলুমবাজি, স্বৈরচারীর পতন, সভ্যতা বিকাশের শর্ত, উচ্চব্যয় হ্রাস, দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ এবং জনগণের জন্য শাসন আর রাষ্ট্রের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং নৈতিক অধঃপতন রোধ করার উপায় সমূহ নিয়ে বিজ্ঞ সমাধানের জন্য রয়েছে দিক-নির্দেশ, পথসন্ধান। এইখানেই তাঁর গবেষণা আর নিরীক্ষণের মাহাত্ম্য। ইবনে খালদুনের মতে, বিশেষ অবস্থা ছাড়া কোনও রাষ্ট্রেরই বয়স সাধারণত একশত কুড়ি বৎসরের বেশি হয় না। রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ও ধ্বংসের অন্যতম জোরালো কারণ হিসেবে অন্যায়-অবিচার বা বে-ইনসাফের প্রসঙ্গ তুলে শাসকগোষ্ঠীকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন খালদুন।
সমাজবিজ্ঞান-এর উদগাতা
ইবনে খালদুন সমাজতত্ত্বেও (আল্-উমরান) জনক। তিনি জীবিকা উপার্জনের উপায়, সম্পদ বণ্টন, বাণিজ্য সরবরাহ, চাহিদা, একচেটিয়া ব্যবসা, মজুতদারি, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক কাঠামোর নানান শ্রেণি বিন্যাস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আর আলোচনা তাঁর ‘আল্-উমরান’ (সমাজবিজ্ঞান)-এ হাজির করেছেন।
অন্যবিধ সাহিত্য নির্মাণ
ইবনে খালদুনের সমসাময়িক অন্য একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনুর খাতিবের রচনা থেকে জানা যায়, ইবনে খালদুন সুবিখ্যাত ‘কাশিদা-ই-বুরদা’ নামক একটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। ইবন রুশদ-এর বহু গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসারও তিনি রচনা করেছিলেন। ফখরুদ্দিন রাজি-র তর্কবিদ্যার কেতাব ‘আল্-মুহাশাল’-এর সংক্ষিপ্তসার এবং অঙ্ক শাস্ত্রের উপর একটি গ্রন্থও সৃষ্টি করেছিলেন। শরিয়ত-এর নীতিমালার উপর নির্ভর করে একটি কাব্যগ্রন্থেরও প্রণেতা ইবনে খালদুন।
ইউরোপে ইবনে খালদুন
সতেরো শতক থেকে ইউরোপীয় বিদ্বৎসমাজ ইবনে খালদুন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচনাবলির অনুবাদ হতে থাকে। উপরন্তু তাঁর সম্পর্কে আধুনিক ইউরোপে বিবিধ পর্যালোচনা হতে শুরু করে তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে সর্বপ্রথম খালদুনের জীবনী প্রকাশিত হয়। ‘দ্য হারবেল্টের বিবলিওগ্রাফি’: ওরিয়েন্টাল। ১৮০৬ এবং ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি প্রাচ্যবিদ স্যাভেস্টার দ্য সাকি ইউরোপে ইবনে খালদুনকে পরিচিত করে তোলেন তাঁর জীবনীগ্রন্থ রচনা ও ‘মুকাদ্দামা’-র কিয়দংশ অনুবাদ করে। অস্ট্রেলিয়ার ওরিয়েন্টালিস্ট ডন হ্যামার পার্গস্টল ঠিক একই রকম সময়ে জার্মানি ভাষায় ‘মুকাদ্দামা’র বিভিন্ন অংশের অনুবাদ করেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ‘জার্নাল এশিয়াটিক’ উপরোক্ত গ্রন্থটির পর্যালোচনা প্রকাশ করে। এই সময়েই কোয়াট্রি মেয়ার-এর উদ্যোগে ‘মুকাদ্দামা’ গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ আরবি টেক্সট প্রকাশিত হয়। ইবনে খালদুনের চিন্তাধারার প্রভাবে ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ জীবিত হয়ে ওঠে। মহাপণ্ডিত-দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের নয়া অভিনব পরিচয় ইউরোপকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। লক্ষ্যযোগ্য হয়ে উঠল এই বিষয়টি যে প্রায় এক শতাব্দী পরে ইতালির ঐতিহাসিক আর রাষ্ট্রবেত্তা নিকোলাই ম্যাকিয়া ডেলি (১৪৫৯-১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ, মতান্তরে ১৪৬৯-১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর ‘প্রিন্স’ নামক গ্রন্থে (১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ) ইবনে খালদুন-এর তত্ত্ব ও মতবাদ নিয়ে ব্যাপক আর পূর্ণতর আলোচনা করেছেন গভীরতর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। ভিকো, ইতালীয় দার্শনিক ঐতিহাসিক (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রিঃ), মঁতেস্কু, ফরাসি দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ (১৬৬৯-১৭৫৫ খ্রিঃ), অ্যাডাম স্মিথ, ইংরেজ অর্থনীতিবিদ (১৭২৩-১৭৯০ খ্রিঃ) এবং অগাস্ট কোঁতে, ফরাসি দার্শনিক (১৭৯৮-১৮৫৭ খ্রিঃ) ইবনে খালদুনের নীতি ও তত্ত্বাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। এসব তথ্য আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা আজ স্বীকার করে নিয়েছে যে যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনার অবতারণা করার কৃতিত্ব ইবনে খালদুনের প্রাপ্য। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে, অস্ট্রেলিয়ার ওরিয়েন্টালিস্ট ডন ক্রোয়ার ‘ইবনে খালদুন এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর ইতিহাস’ (বঙ্গানুবাদ) নামক গ্রন্থ, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে পেশ করেন। সেই গ্রন্থে ইবনে খালদুনকে তিনি ‘কালচারাল হিস্টোরিকা’— সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক অভিধায় ভূষিত করেন। ওলন্দাজ পণ্ডিত ডি. বোয়ের; খালদুন-এর অনুপম চিন্তাশক্তির প্রশংসা করেছেন। ইবনে খালদুন ধর্মকে ব্যক্তিজীবনের বিষয় হিসেবে দেখেছেন। তাঁর দর্শন, সমাজবিজ্ঞানকে যুক্তি আর অবধারণভিত্তিক মন দিয়ে দেখেছেন। ঠিক যেমন অ্যারিস্টটল আর প্লেটো-র (আফলাতুন) মতবাদে ধর্মীয় প্রভাব অনুপস্থিত ছিল। অধ্যাপক ডি. বোয়ের সাহসের সঙ্গে একটি মন্তব্য করেছেন, ‘কোন পূর্ববর্তী মনীষীকে অনুসরণ না করেই যে প্রতিভাটির আবির্ভাব ঘটেছিল, সে প্রতিভাকে অনুসরণ করতে মুসলিম সমাজে কেউ এগিয়ে আসেনি। ১৯০১-এ এই বিশ্লেষণটি করেছিলেন অধ্যাপক বোয়ের। ইবনে খালদুনের বর্ণনায় জীবনের অবসান হয়েছিল ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ। ইবনে খালদুন ছিলেন মুসলিম জাহানের গর্ব।


All Rights Reserved © Copyright 2025 | Design & Developed by Webguys Direct