X


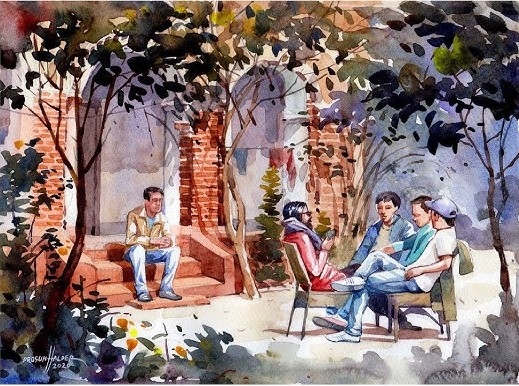
পাভেল আখতার: লেখক মাত্রেই ভাবুক, নিঃসন্দেহে। ভাবনা ছাড়া কি লেখা যায়? যায় না। অসম্ভব, অভাবনীয়। জীবন ও জগৎ-কে দেখা, শুধু বাইরের দৃষ্টি দিয়ে নয়, অন্তর্দৃষ্টি দিয়েও, একজন লেখকের ভাবনার সমুদ্রে ঢেউ তোলে। ঘটমান ও পুরাঘটিত--দুটিকেই তিনি দেখেন স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে, আর পাঁচজন মানুষ যখন নিয়তিতাড়িত বা নিয়তিচালিত হয়ে তার মধ্যে আবর্তিত হন, একজন লেখক তখন ঘটনাটিকে আপন মনে ও মননে বিশ্লেষণ করেন এবং তার মধ্যে নতুন ব্যঞ্জনা সংযোজনের প্রয়াস পান। অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি--দুটোই একজন সৃষ্টিশীল লেখকের আত্মগত বৈশিষ্ট্য।
বিশ্বচরাচরে সতত বহমান অনন্ত শক্তিপ্রবাহ। যেভাবে গাছে ফুল ফোটে, বাতাস বয়ে যায়, সূর্য ওঠে আবার অস্ত যায়, প্রাণের ভিতরে আরেকটি প্রাণ জ্ঞানাতীত বিস্ময়ে জন্ম নেয় ও ক্রমবর্ধিত হয় এমন অজস্র বিষয় আমাদের বিরাট, আকুল জিজ্ঞাসার সামনে এনে দাঁড় করায়! অগণন বস্তুপুঞ্জ, কালপরিধি, নিপাট ও নিটোল নিয়মের বৃত্তে আমার অবস্থান কী এবং কেন--এই আদি প্রশ্নজড়িত ভাবনার জাল বুনতে মন আপনাআপনি ব্যগ্র হয়ে ওঠে! বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু নিত্য বহমান নদীটির তীরে বসে আপনমনে একদা এই গূঢ় প্রশ্নটি করেছিলেন : ‘’ভাগীরথী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?” আবার রবীন্দ্রনাথের মনে গুঞ্জরিত হয়েছে--”জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে, ভাসালে আমারে জীবনেরও স্রোতে!” সৃষ্টিপ্রবাহের বিচিত্র ও বিস্ময়কর গতিপথ, তার উৎস ও গন্তব্যের অভিমুখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হওয়া, গভীর ভাবনায় মগ্ন হওয়া! ‘’সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর’’, কিংবা ‘’এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে’’ গানে বিস্ময়কর প্রজ্ঞাধৃত অনুভব থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন কে কখন কার পিছনে পড়ছে! ‘আমি’ তো রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু, ‘তুমি’ কে? আহা! এবং, সেজন্যেই বোধহয় তিনিই পরম প্রশান্তিতে লিখতে পারেন--”তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই...!” একজন লেখকের ভাবুকতায় হিরণ্ময় মহিমার স্বর্ণপরশ লাগে! যুগে যুগে, কালে কালে ‘মহান লেখকের’ শিরোপাও নিকটে আসে!
একজন লেখকের মূল অবলম্বন ভাবুকতা। কিন্তু, ভাবতে হবে, সেটাই কি একজন লেখকের বড় গুণ? সাবেক আমলে জমিদার বাড়িতে যিনি ‘হিসেব’ লিখতেন তিনি কি ‘লেখক’ পদবাচ্য বলে গণ্য হতেন? তারও তো কাজ ছিল ‘লেখা’ই। যাকে আমরা ‘লেখক’ বলি তার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে : ‘সংবেদনশীলতা’। জীবন ও জগৎ-কে তিনি পঙ্কিল ও বঙ্কিম দৃষ্টিতে দেখেন না। আগে তিনি নিজের দৃষ্টি ও চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন করেন। জীবন ও জগতের প্রতি সব আগে তার অন্তরে গভীর মমত্বের অনুভূতি তৈরি হয়। সংসারে অনেক রকম ও অগণিত ‘পাঁক’ আছে। কিন্তু, সেটা যথার্থরূপে একজন ‘প্রকৃত লেখক’ই চিনতে পারেন। যিনি চিনতে পারেন তার ‘পাঁক’ চেনানোর ধরনেও থাকে ওই মমত্বেরই স্নিগ্ধ ছায়া। কিন্তু, যার দৃষ্টি ও মনন পরিচ্ছন্ন ও প্রসারিত নয় তিনি যেখানে ‘পাঁক’ দেখেন তা আসলে তার অন্তর্গত সত্তারই প্রতিরূপ। তার কাছ থেকে ‘সংবেদনশীলতা’র বিচ্ছুরণ আশা করা ভুল। একজন ‘লেখক’-কে আগে শিখতে হয় কীভাবে দেখবেন, কীভাবে ভাববেন। এই প্রক্রিয়া থেকে দূরে অবস্থান করলে কাউকে ‘লেখক’ বলা তো যায়-ই না, উপরন্তু তিনি যদি কিছু লেখেনও তাহলে সেটা গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়ায়!
আবার মেধা, পাণ্ডিত্য ও ভাবুকতার শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হলে তখন সব সীমারেখা, চিহ্ন বা গোত্র নির্মাণই যেন লুপ্ত হয়ে যায়! প্রান্তবর্গীয় ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য রণজিৎ গুহ। তিনি মূলত প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। কিন্তু, তিনি যখন লিখছেন ‘কবির নাম ও সর্বনাম’ কিংবা ‘ছয় ঋতুর গান’ তখন ভাবনাতীত হয়ে ওঠে যে, ‘আলো’ ঠিক কোথা থেকে আসছে! আরেক দিকপাল ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী যখন পরিবেশ নিয়ে গভীরতর ভাবনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন তখন তা-ও বিস্ময়কর না হয়ে পারে না! আবার স্বনামধন্য পদার্থবিজ্ঞানী পলাশ বরন পাল প্রিয় বাংলা ভাষার শ্যামল অরণ্যে, অথবা বলি, অলিতে-গলিতে যেভাবে হেঁটে বেড়ান আর সেই মেধাবী ভ্রমণ ছড়িয়ে দেন তাঁর স্নিগ্ধ, রম্য সব গদ্যে তখনও অভিভূত হতে হয়!
বেশ। কিন্তু, ‘গোল’ বাধে একটি জায়গায় এসে। যিনি পরিচিত হন ‘ধর্মতাত্ত্বিক’ হিসেবে, বাজারে তাঁর মেধা ও পাণ্ডিত্যের বেশি ‘দাম’ ওঠে না! দশম শতাব্দীর ইমাম গাজ্জালীকে সবাই হয়তো ‘ধর্মতাত্ত্বিক’ই বলবেন। কিন্তু, তিনি কি দার্শনিকও নন? ইবনে খালদুনকে আমরা কি শুধুই ‘ইতিহাসবিদ’ বলব? তিনিও কি একদিক থেকে দেখলে ধর্মতাত্ত্বিক নন? কিংবা, যদি বলি তিনি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও? আল-বিরুণীকে তো কোনও একটি বিশেষ পরিচয়ে চিহ্নিত করা সম্ভবই নয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী, চিন্তাবিদ মৌলানা আবুল কালাম আজাদকেও হয়তো ‘ধর্মতাত্ত্বিক’ বলা হবে! স্বামী বিবেকানন্দ বা ঋষি অরবিন্দও কি তাহলে শুধুই ‘ধর্মতাত্ত্বিক’? যিনি সব মেলাতে পারেন তিনি আকাশ ও মাটিকে একসূত্রে গাঁথেন! আমরা মেলাতে পারি না। তাই আমরা একটি সংহত পুষ্পমালাকে দেখতে পারি না, শুধু দু’একটি ফুল দেখি। ‘জগৎসভা’ সমগ্রতার নাম। কিন্তু, বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই আমরা জগৎসভাকে দেখি। আমাদের চিন্তার এই দৈন্য কবে ঘুচবে জানি না!
‘ইতিহাসবিদ’ শব্দটি যেসব ব্যক্তি ও তাঁদের চিন্তাপথকে চিহ্নিত করে তা সাধারণ পাঠকের দিক থেকে দেখতে গেলে খুবই সরল। কেবল রাজকীয়তার আনাচকানাচ নয় ; সমাজ যে স্রোতরেখা ধরে বয়ে চলেছে তা এবং তার থেকে শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন কোনওটাই বিচ্ছিন্ন নয়। একজন আদর্শ মেধাবী ভাবুক তিনিই, যিনি সবকিছুর সঙ্গেই নিজেকে গ্রথিত করেন। তার বৃহৎ ‘ভাবনাবিশ্ব’ সবকিছুকেই গ্রহণ করে। এবং, তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ও নির্মোহ মনে সেসব বিশ্লেষণ করেন। তাকে কি উপরিউক্ত সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ করে ফেলা যায়? একদমই নয়। তপন রায়চৌধুরী কি কেবল ‘ইতিহাসবিদ’? যে অসামান্য ও মনোমুগ্ধকর গদ্যে তিনি তাঁর অনন্য মেধা ও মননকে নানা দিগন্তে বিচ্ছুরিত করে গেছেন তা শুধু আমাদের ঋদ্ধ করে না, আলোকিতও করে!
রণজিৎ গুহ---এই মানুষটির পরিচয় দিতে গিয়ে যদি কেবল বলা হয়--’পিছড়ে বর্গের ইতিহাসচর্চার পথিকৃৎ’, তাহলে বোধহয় কিছুই বলা হয় না তাঁর সম্পর্কে ; অন্তত, তাঁর ‘কবির নাম ও সর্বনাম’ বইটি পড়া থাকলে। কিংবা, ‘ছয় ঋতুর গান’। আরও কত বই! জ্ঞানচর্চার বিচিত্র সব ঘাটে ঘাটে তাঁর অবাধ বিচরণ! আর গদ্য? ধ্রুপদী সৌরভ মিশে আছে তাঁর অনবদ্য গদ্যশৈলীতে! ‘পড়াশুনা’ যে মুক্ত পৃথিবীর যেখানে যত ‘রস’ আছে তা আহরণ ও আস্বাদন করা, তার একটি উজ্জ্বলতম নমুনা হ’ল এই বই--’কবির নাম ও সর্বনাম’, যেখানে একজন স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ তাঁর অতল, গভীর কাব্যপাঠের মধ্য দিয়ে কাব্যের অনাবিষ্কৃত একটি দিগন্ত উন্মোচন করেছেন! প্রচলিত অর্থে তিনিও তো খ্যাতিমান এক ‘ইতিহাসবিদ’, কিন্তু সেই একমাত্রিকতা দিয়ে কি তাঁর দুরন্ত মেধা ও পাণ্ডিত্যের দীপ্তিকে সীমায়িত করা যায়? দিনান্তে তাঁকে বলা যায় মেধা ও পাণ্ডিত্যের বৃত্ত ভাঙা এক আশ্চর্য চিন্তাপথিক! তপন রায়চৌধুরী ইতিহাসকে সাহিত্য হিসেবে পড়তে চেয়েছিলেন। আবার রণজিৎ গুহ সাহিত্যকে পড়তে চেয়েছিলেন ইতিহাস, রাজনীতি ও প্রজ্ঞাময় দর্শন হিসেবে।
৩১ অক্টোবর, ২০২১-এ দৈনিক ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘ছুটি’-তে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ চিন্ময় গুহ’র অসামান্য একটি ‘খনন’ ছিল ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্রকে নিয়ে। ‘আমি গৌতম ভদ্রকে খুঁজছি’। ‘ইতিহাসবিদ’--এই একটি মাত্র পরিচয়ে তাঁর মতো অনন্য জ্ঞানতাপস ব্যক্তিকেও ‘ধরা’ খুবই মুশকিল। বটতলার পুঁথি থেকে শুরু করে হযরত মহম্মদ (স)--জ্ঞানচর্চার কত বিচিত্র পথে তাঁর পরিভ্রমণ! জ্ঞানতপস্বী গৌতম ভদ্র চিন্ময় গুহর অপরূপ লিখনে বলছেন : ‘’পড়ার লোভ ছেড়ে লিখতে খারাপ লাগে। আমি সৌভাগ্যবান। বই পড়তে ও পেতে খামতি হয়নি। কিনে পড়েছি। নানাভাবে পড়েছি। আজও পড়ি। ইচ্ছেমতো। উদ্দেশ্যহীন পড়াশুনা আমাকে পণ্ডিতির হাত থেকে বাঁচিয়েছে...।’’ কী কথা! ভাবা যায়! যদিও আমরা তাঁকে ‘পণ্ডিত’ বলতে কোনও দ্বিধাই বোধ করব না, সে তিনি নিজের সম্পর্কে নিজে যা-ই বলুন! ‘পড়ার লোভ ছেড়ে লিখতে খারাপ লাগে’--শ্রী ভদ্রের এই কথাটি চিত্তাকর্ষক! ‘আদর্শ পাঠক’ বলে কিছু কি হয়? যে সবই ভালবাসে, যে সবই পড়ে ; বাছবিচার করে না। কিন্তু, কারও পছন্দ ধর্ম, কারও রাজনীতি, কারও শিল্প-সংস্কৃতি, কারও জিনতত্ত্ব, কারও অজিনতত্ত্ব, কারও ইতিহাস, কারও পাতিহাঁস ইত্যাদি। ‘আদর্শ পাঠক’ খুঁজে পাওয়া বড্ড দুষ্কর, যার কি না সবকিছুতেই ‘রুচি’ আছে। আসলে সমস্যাটা ‘পরিপাকযন্ত্রের’। সবই ‘হজম’ হয়, এমনকি লোহাও, ফলে সবই খেতে পারতেন দেদার, এমন মানুষ যেমন বিরল হয়ে পড়েছে, তেমনই হয়তো পাঠকও! তবে, এখনও কিছু মানুষ, না পাঠক আছেন, যাদের ‘আদর্শ পাঠক’ বলা-ই যায়।
উপরিউক্ত কয়েকজনের মতো আরও অনেকেই অতীতে ছিলেন, যাঁরা আদর্শ পাঠক, মেধাবী ভাবুক ও লেখক ; কেবল ওই কয়েকটি নামই যথেষ্ট নয়। তাঁদের মধ্যে অন্তত আরও চারটি নাম অবশ্যই বলতে হবে। শিশির কুমার দাশ, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, সুধীর চক্রবর্তী এবং রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত। মেধা, পাণ্ডিত্য, ভাবুকতা হচ্ছে মূলত বহুস্তরীয় শব্দ! সাতরঙা রামধনুর মতো!


All Rights Reserved © Copyright 2025 | Design & Developed by Webguys Direct